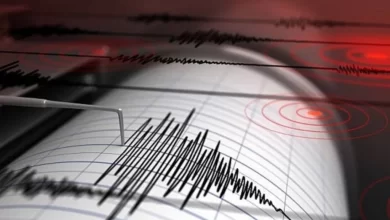বিচার বিভাগের কর্তৃত্ব সুপ্রিম কোর্টের হাতে

অনলাইন ডেস্ক: অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা ন্যাস্ত হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের হাতে। আদি সংবিধানে এই ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের হাতে থাকলেও চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এই ক্ষমতা দেওয়া হয় রাষ্ট্রপতির হাতে। পরে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে তাতে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শের বিষয়টি যুক্ত করা হয়।
যার মধ্য দিয়ে বিচার বিভাগে দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে বিরাজ করছিল দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা। আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগের প্রচ্ছন্ন প্রভাব ছিল বিচার বিভাগের উপর। উচ্চ আদালতের এক রায়ের মধ্য দিয়ে অবসান হলো দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার। যে রায়ে বিদ্যমান সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদকে সংবিধান পরিপন্থি ঘোষণা করে হুবহু পুনর্বহাল করা হয়েছে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ। বিচারপতি আহমেদ সোহেল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর দ্বৈত হাইকোর্ট বেঞ্চ মঙ্গলবার এই ঐতিহাসিক রায় দেন।
রায়ে তিন মাসের মধ্যে বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করতে সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বাতিল করা হয়েছে অধস্তন আদালতের বিচারকদের জন্য ২০১৭ সালে প্রণীত শৃঙ্খলা বিধিমালাও। যে বিধিমালায় নিম্ন আদালতের বিচারকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বকে খর্ব করা হয়েছিল। যা উঠে এসেছে হাইকোর্টের রায়ের পর্যবেক্ষণে। এদিকে এই রায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি আপিল করার সার্টিফিকেট ইস্যু করেছে হাইকোর্ট। অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয় জানিয়েছে, রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে।
রায়ের পর রিটকারী পক্ষের কৌঁসুলি অ্যাডভোকেট মো. শিশির মনির বলেন, এই রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হলো। একই সঙ্গে এই রায়ের মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব এবং রাজনৈতিক প্রভাব থেকে আমাদের অধস্তন বিচার বিভাগ মুক্তি পেল। আত্মমর্যাদা ও সম্মান ফিরে পেলেন অধস্তন আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা। তিনি বলেন, এই রায়ের মাধ্যমে দেশের বিচার ব্যবস্থায় যে অনিশ্চয়তা আছে, যে প্রভাব আছে, তা মুক্ত হবে। এই রায় বাস্তবায়ন হলে বিচার বিভাগের ওপর দুষ্টচক্রের যে প্রভাব আছে, তার অবসান হবে। রায়ের মধ্য দিয়ে চেক এবং ব্যালেন্স প্রতিষ্ঠিত হলো। ফলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নামে আইন মন্ত্রণালয়ের হাতে আর কোনো ‘নাটাই’ থাকলো না। ‘নাটাই’ পরিপূর্ণভাবে সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত থাকল। নির্বাহী বিভাগ আর ছড়ি ঘুরাতে পারবে না।
মামলার অ্যামিকাসকিউরি ড. শরীফ ভূঁইয়া বলেন, হাইকোর্টের রায়ে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল হয়েছে। ফলে অধস্তন আদালতের কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ সুপ্রিম কোর্টের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। যেহেতু ১১৬ অনুচ্ছেদ পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল, সেহেতু পরিবর্তিত ১১৬ অনুচ্ছেদের আলোকে করা শৃঙ্খলাবিধি বাতিল করা হয়েছে।
হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ :
হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অংশ। সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিপন্থি কোনো আইন সংসদ প্রণয়ন করতে পারে না। যদি এমন আইন করা হয়, তবে তা অসাংবিধানিক ঘোষণা করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে। রায়ে বলা হয়েছে, সংবিধান সাধারণ কোনো আইন নয়। সংবিধানের কোনো বিধানকে যখন অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হয়, তখন পূর্ববর্তী বিধান স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরুজ্জীবিত বা পুনর্বহাল হয়ে যায়। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী মামলাসহ ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংবিধানিক মামলার রায়ে এই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে।
রায়ে হাইকোর্ট বলে, মামলার শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষ দাবি করেছিল- বিদ্যমান সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ বাতিল করা হলে ‘চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স’ নষ্ট হবে। আমরা মনে করি এমন যুক্তি সঠিক নয়। সংবিধানে বলা আছে নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত থাকবে বিচার বিভাগ। এছাড়া রাষ্ট্রের তিন অঙ্গের (আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ) মধ্যে ক্ষমতার যে পৃথকীকরণ নীতি, বিদ্যমান সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ সেই নীতিকে খর্ব করেছে। কারণ, রাষ্ট্রের তিন অঙ্গের একটি আরেকটির ওপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ নাই। এ কারণে আমরা মনে করি, বিদ্যমান সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ অসাংবিধানিক ও আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত। এজন্য তা বাতিল ঘোষণা করা হলো। একই সঙ্গে আদি (বাহাত্তরের) সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল হলো।
হাইকোর্ট বলে, ২০১৭ সালে তত্কালীন সরকার অধস্তন আদালতের বিচারকদের শৃঙ্খলা বিধিমালা প্রণয়ন করে। রিটকারীদের দাবি, সরকার রাজনৈতিক স্বার্থে সুপ্রিম কোর্টে শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃর্তৃত্বকে ক্ষুণ্ন করে এই বিধিমালা প্রণয়ন করেছিল। অথচ এই বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল সুপ্রিম কোর্টের। মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আলোকে অধস্তন আদালতের বিচারকদের শৃঙ্খলাবিধি প্রণয়ন না করায় ঐ শৃঙ্খলাবিধিমালাকে অসাংবিধানিক ও বাতিল ঘোষণা করা হলো।
পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার রায়ে হাইকোর্ট বলেন, জাতীয় সংসদ ও নির্বাচন কমিশনের পৃথক সচিবালয় রয়েছে। কিন্তু বিচার বিভাগের স্বতন্ত্র সচিবালয়ের কথা মাসদার হোসেন মামলায় রায়ে উল্লেখ থাকলেও আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। যা সুপ্রিম কোর্টের রায়ের লঙ্ঘন। পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খোদ রাষ্ট্রের শীর্ষ আইন কর্মকর্তা কোনো আপত্তি আদালতে দেননি। বিচার বিভাগ ও সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনেও পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এই সচিবালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ৩১টি রাজনৈতিক দল ঐকমত্য পোষণ করেছে। সুতরাং আমরা মনে করি, বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত রাখতে পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার এখনই উপযুক্ত সময়। ফলে বিবাদীদের নির্দেশ দেওয়া হলো- সুপ্রিম কোর্টের প্রস্তাবনা অনুসারে রায়ের অনুলিপি পাওয়ার তিন মাসের মধ্যে পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করতে।
ফিরে দেখা :
১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে অধস্তন আদালতের দায়িত্ব পালনরত বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি দান ও ছুটি মঞ্জুরিসহ) শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত ছিল। ১৯৭৪ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত করে। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই ক্ষমতার প্রয়োগ হবে-শব্দগুলো সন্নিবেশিত করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ পঞ্চম সংশোধনী আইন অসাংবিধানিক মর্মে ঘোষণা করলে পঞ্চদশ সংশোধন আইন, ২০১১ এর মাধ্যমে ১১৬ অনুচ্ছেদের বর্তমান একই বিধানটি প্রতিস্থাপন করা হয়। এই ১১৬ অনুচ্ছেদের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন অ্যাডভোকেট সাদ্দাম হোসেনসহ ১০ জন আইনজীবী। রিটের উপর একগুচ্ছ রুল জারি করে হাইকোর্ট। রুলের উপর রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ও অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক, রিটকারী পক্ষে শিশির মনির, ইন্টারভেনর হিসেবে আহসানুল করিম ও ড. মহিউদ্দিন, অ্যামিকাসকিউরি হিসেবে ড. শরীফ ভুইয়া শুনানি করেন।